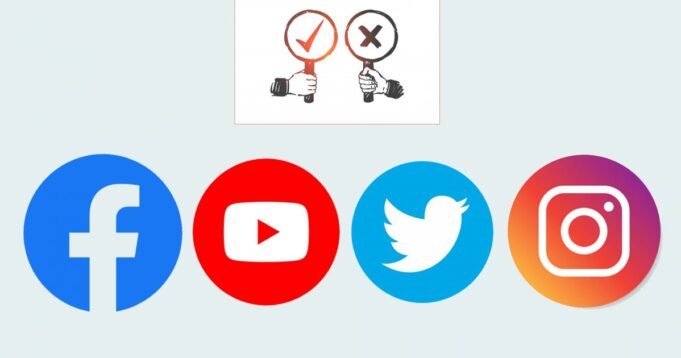নির্বাচনী পরিবেশে আপনি কি সোশ্যাল মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত?
নির্বাচনী পরিবেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সত্য-মিথ্যা তথ্য। অসমর্থিত উৎস থেকে বিভিন্ন ভিডিও ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিউবে প্রচারিত হয়েছে। সত্যের সামনে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়া মিথ্যা তথ্য নাগরিকরা কীভাবে মোকাবেলা করবে তা হল বড় প্রশ্নটি সামনে এসেছে। যারা ফ্যাক্ট চেকিং করছেন তারা বলছেন, প্রোপাগান্ডার পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় পুরো বিষয়টিকে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের আওতায় আনা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ প্রচারই নিয়মতান্ত্রিক ফ্যাক্ট-চেকিং ছাড়াই নির্বিচারে, ঘৃণা-উৎসাহমূলক। এই ধরনের তথ্য বিশ্বাস করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের আইসিটি বিভাগ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাইবার মনিটরিং সেল গঠন, ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং জাল সংবাদ বিরোধী উদ্যোগ এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হওয়া। কিছু ইউটিউব চ্যানেল নিজেদের ‘নিউজ চ্যানেল’ হিসেবে উপস্থাপন করলেও বাস্তবে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দলীয় প্রচারণা চালায় বা ভুয়া তথ্য ছড়ায়। অ্যালগরিদম অপব্যবহার করা হয়. YouTube-এর অ্যালগরিদম এমন ভিডিও দেখায় যা আরও বেশি লোকের কাছে দ্রুত ভিউ পায়৷ ফলে ভুয়া তথ্য দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। সতর্ক থাকা জরুরী।
মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক সুদীপ্ত সালাম এআই এবং ইউটিউব কেন্দ্রিক অসাংবাদিকতাকে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমানে আমরা দেখছি এআই নিয়ে তৈরি বিভিন্ন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। অনেকেই সেই ভিডিওগুলোর তথ্যকে সত্য বলেও বিবেচনা করছেন। সেই ভিডিওগুলো অবিলম্বে নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতি দিন দিন বাড়ছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়বে। অন্যদিকে, ইউটিউব-ফেসবুক-কেন্দ্রিক ডিসইনফরমেশন প্ল্যাটফর্মগুলি যেগুলি বাণিজ্যিক ধারণার নামে বিকাশ লাভ করেছে তারা অভিশাপের মতো কাজ করছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতার নৈতিকতাকে সম্মান করা হয় না। ক্যামেরা, বুম এবং মোবাইল ফোন কাউকে দেওয়া হয়। তারা সাংবাদিকতা কি তাও জানে না। তিনি শুধু জানেন যে তাকে এমন কিছু ক্যাপচার করতে হবে যা লক্ষ লক্ষ ভিউ থাকবে।
সুদীপ্ত সালাম বলেন, ‘ভিডিও টেক্সটের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রভাব ফেলে। সাংবাদিক হলে ভিডিওর মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, অসাংবাদিক হলে মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক ও বানোয়াট বিষয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। মূলধারার মিডিয়ার কাছাকাছি নাম, ইউটিউবে ভুয়া চ্যানেল এবং ব্যঙ্গ ও অপপ্রচার সম্বলিত পোস্টের ভুয়া পৃষ্ঠাগুলির বিস্তার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে কোনো তথ্য যাচাই না করেই শেয়ার করার প্রবণতা রয়েছে।
সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ তানভীর হাসান জোহাকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ভয় তৈরি করে, কখনও কখনও ব্যক্তিগত সম্মান বা নিরাপত্তার ক্ষতি করে।’ অতএব, শেয়ার করা হয়নি এমন কোনো তথ্য অবিলম্বে বন্ধ করা এবং যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। উৎস কোথা থেকে এসেছে, তারিখটি পুরনো নাকি নতুন, একই তথ্য একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় কিনা—এই তিনটি বিষয় যাচাই করলে অনেক ভুল এড়ানো যায়। আবেগ দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে কথা বলা আমাদের দায়িত্ব। কারণ আমাদের তথ্যের বাহক হওয়া উচিত, ভয় নয়।
‘কোনটি মূলধারার মিডিয়া এবং কোনটি নয় – ভয়েস ওভার, ভিডিও উপস্থাপনা দিয়ে, শিশু অধিকার কর্মী এবং সাইবার নিরাপত্তা সামাজিক বিশ্লেষক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, আজকাল এটা বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে৷ ‘এই মুহুর্তে যখন এআই এসেছে, অনলাইন ব্যবহারকারীরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। কেউ কেউ বোঝে না জাল কী, কেউ যা দেখে তা বিশ্বাস করে এবং কেউ সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়। যেহেতু ভিডিও এবং চিত্রগুলি এখন পরিবর্তন করা যেতে পারে, ফলে আশঙ্কা বেশি। সাবধান হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে ‘থিঙ্ক’ পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলা হয়। কিছু শেয়ার করার আগে যাচাই করে নিন যে এটি সত্য কিনা, সহায়ক (এটি কারও কাজে লাগবে), তথ্যমূলক (এটি কি তথ্যপূর্ণ), নেতিবাচকতা (এটি কি সত্য কিন্তু শেয়ার করা সময়োপযোগী), দয়া (যেভাবে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে)। যা বলতে হবে তা হল, আপনি যা বোঝেন না তা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।’
নির্বাচনের আগে ও সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য রোধে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইসিটি বিভাগের একজন কর্মকর্তা এর উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, ‘অতীতেও আইসিটি মন্ত্রণালয় এবং সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা তথ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে সাংবাদিকদের ডিজিটাল ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। যাতে তারা ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তি সনাক্ত করতে পারে এবং এই ধরণের প্রসারিত কাজ করতে পারে। এ জন্য আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অনেক লোককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে, এবং একই সাথে, আইসিটি মন্ত্রণালয় সরাসরি এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে কিভাবে এই ভুল তথ্যটি গভীরভাবে জাল, কীভাবে মানুষকে তাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করা যায় এবং কীভাবে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। সরকারের স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিং এবং অ্যাকশনেবল ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা তথ্য যাচাই করে এবং নিরপেক্ষ রায় দেয় – কোনটা সত্য, কোনটা বিকৃত, কোনটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটি জনগণের আস্থা বাড়ায় এবং গুজবের প্রভাব হ্রাস করে। অনেক সংস্থা, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হোক বা স্বাধীনভাবে, এখন নিয়মিত সত্যতা যাচাই করছে। কিন্তু কী পরিমাণ বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তা যাচাই করার ক্ষমতা আছে কি?
ডিজিটালি রাইট-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিরাজ আহমেদ চৌধুরী বিশ্বাস করেন যে অনলাইনে পাওয়া ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে, যারা এই মুহূর্তে সত্যতা যাচাই করছেন তাদের এটি যাচাই করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নেই। এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, জনবল কম, প্রচার বেশি। দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যম পদ্ধতিগতভাবে ঘটনা তদন্ত করতে পারে না। কারণ, আপনি যা যাচাই করতে চান তাতে অবশ্যই যাচাইযোগ্য ভুল তথ্য থাকতে হবে। অনলাইনে যা কিছু ছড়ায় তা হল গুজব, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, ঘৃণা, কোন তথ্য নেই। মতামতগুলি এমন মতামত যা যাচাই করা যায় না। তিনি বলেন, ‘মিডিয়ার কাজ আগে ছিল তথ্য দেওয়া, এখন বলতে হবে কোন তথ্য মিথ্যা। তাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এখানে বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু শুধু যাচাই বা অনুসন্ধান করে এই ভুল তথ্য বন্ধ করা যাবে না, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেরও দায়িত্ব রয়েছে। অধিকার লঙ্ঘন না করেই এগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দিনের শেষে, মানুষের বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কী নিতে হবে এবং কতটা নিতে হবে তা বোঝা ভুল তথ্য প্রতিরোধের একটি উপায়। এটি বিকাশের জন্য, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা যুক্ত করতে হবে।
(ট্যাগস্টোট্রান্সলেট)বাংলাদেশ(টি)সংবাদ
প্রকাশিত: 2025-11-09 01:54:00